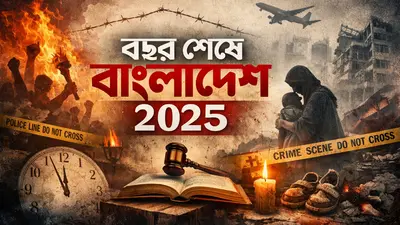জন্মশতবর্ষে ঋত্বিক ঘটক
ঋত্বিককে বাংলাদেশের ভালোবাসতেই হবে!

১
ঋত্বিক ঘটক। বাংলার ক্ষ্যাপা পরিচালক। তার ক্ষ্যাপামিকে ভয় পেতেন না, তার সমসাময়িক এমন কোনো বুদ্ধিজীবী কোলকাতায় ছিলেন না। সত্যজিৎ রায়ও তার হাত থেকে নিস্তার পাননি। একবার গভীর রাতে বাড়ি ফিরে ট্যাক্সি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সোজা সত্যজিতের বাসায়। ‘ও বাড়ি যাও, এক লম্বা ঢ্যাঙা মতন লোক তোমার ভাড়া মিটিয়ে দিবে।’ তা দিয়েও ছিলেন ‘মানিক বাবু’।
ঋত্বিকের এই ক্ষ্যাপামি কোনো বাতিকগ্রস্ততা ছিল না। সে ছিল শিল্পীর যন্ত্রণা-জর্জর জীবনযাপন। ইতিহাসের এক গভীর ক্ষত বয়ে বেড়ানো শিল্পীর যন্ত্রণা। দেশভাগের যন্ত্রণা। পূর্ববাংলা থেকে তার বিচ্ছিন্ন হয়ে পরার যন্ত্রণা। মাতৃভূমি দুটুকরো হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা। সাংস্কৃতিক জঠর থেকে ছিটকে পরার যন্ত্রণা।
তার শিল্পের, তার শিল্প-ভাষার এক বড় উৎস এই যন্ত্রণা। তিনি যখন সিনেমা বানাচ্ছেন, তখন আর পূর্ব বাংলা তার দেশ নয়। তার দেশের অংশ নয়। সে এক আলাদা দেশ, পাকিস্তান। তার দেশের নাম তখন ভারত। তার রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ। তিনি তবু বলে যাচ্ছেন বাংলার কথা। বাংলাদেশের কথা। কারণ তিনি সিনেমা বানাতেন মানুষের জন্য। মানুষ তো ভাগ হয় না। বাঙালি তো বাঙালিই রয়ে গেছে। এই যন্ত্রণা বার বার তিনি বলেছেন তার সিনেমায়।
২
ঋত্বিক কখনোই দেশভাগকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি তো শুধু সীমান্তের ওপারে চলে যাওয়া একজন শিল্পী নন। তিনি ছিটকে যাওয়া এক আত্মা, যে কখনো ভুলতে পারেনি তার জন্মভূমিকে। বাংলা ভাষা তার কাছে কেবল যোগাযোগের মাধ্যম ছিল না; ছিল তার অস্তিত্বের কেন্দ্র। সেই ভাষার ভূগোল যখন দু’টুকরো হলো, ঋত্বিকের ভেতরটাও যেন ভেঙে গিয়েছিল।
তাই তো “যুক্তি তক্কো আর গপ্পো”-তে নিজের মুখেই উচ্চারণ করেন “বাংলাদেশ”। কী গভীর আবেগ নিয়ে! যেন ভাষার শব্দটুকু নয়, নিংড়ে উচ্চারণ করছেন নিজের ভাঙা আত্মাটাকেই। সেই উচ্চারণে নেই কোনো রাজনীতি, নেই কোনো কোনো রাষ্ট্রচিন্তা, কেবলই মাটির টান। মা মাটি মাতৃভূমির টান। যে মাটি থেকে তিনি ছিটকে গেছেন। ইতিহাসের নির্মমতায় ছিটকে যেতে হয়েছে।
১৯৭১ সালে যখন বাংলাদেশে গণহত্যা চলছে, শুরু হয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধ, তিনি পাশে দাঁড়াতে মুহূর্ত দ্বিধা করেননি। রাস্তায় নেমেছেন, মানুষের কাছে গেছেন, চাঁদা তুলেছেন, সভা সম্মেলন করেছেন। তাকে কাউকে বলে দিতে হয়নি। নিজের কাছে তার উত্তর ছিল স্পষ্ট; বাংলাদেশ তার মাতৃভূমির অর্ধেক। বেদনার অর্ধেক। হৃদয়ের অর্ধেক। ভালোবাসার অর্ধেক? সে বোধহয় পুরোটাই।
৩
স্বাধীন বাংলাদেশ থেকে তিনি যখন সিনেমা বানানোর ডাক পেলেন, তিনি যেন সে জন্যই জীবনভর অপেক্ষায় ছিলেন। ঋত্বিক ঘটকের অনেক বদনাম আছে। কিন্তু আপোষ করার দুর্নাম নেই। সেজন্য তাকে ভুগতেও কম হয়নি। দেশসেরা পরিচালক হয়েও ছবি বানিয়েছেন মোটে আটটা। মুক্তির ফেরে ‘পথের পাঁচালী’র আগে বানিয়েও ‘নাগরিক’ মুক্তি পায় পরে। হাতে ছবি ছাড়া ঘুরে বেরিয়েছেন, তবু আপোষ করেননি। সেটা অর্থনৈতিক হোক, নান্দনিক, বা রাজনৈতিক। প্রধানমন্ত্রী নিজ আগ্রহে তাকে চলচ্চিত্রের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে বড় পদে আসীন করেছিলেন বারবার। সেই এক কারণে ধরে রাখতে পারেননি।
সেই ঋত্বিক বাংলাদেশে ছবি বানাতে গিয়ে প্রযোজকের শর্ত মেনে নিলেন। অবশ্য শর্তটাও বাংলাদেশ নিয়েই। কলাকুশলী নির্বাচনে অগ্রাধিকার দিতে হবে বাংলাদেশের শিল্পী-কুশলীদের। এর আগে-পরে এর অন্য উদাহরণ আছে কিনা ঘোরতর সন্দেহ।
কারণ বোধহয় সেই—তার কাছে বাংলাদেশ কোনো ছিন্ন ভৌগোলিক সত্তা নয়, ছিল ব্যক্তিগত বিশ্বাসের অংশ। এ মাটি তার নিজের মাটি। হয়তো ‘তিতাস একটি নদীর নাম’ দিয়ে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন তার জন্মভূমির কাছে।
৪
কেবল ঋত্বিক নয়, বাংলাদেশের সঙ্গে গভীর বাধনে বাধা ছিল তার পুরো পরিবার। তার যমজ বোন প্রতীতি দেবী ছিলেন কুমিল্লার দত্ত পরিবারের পুত্রবধূ। সেই ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পরিবার, যিনি পাকিস্তানের গণপরিষদে প্রথম বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলেছিলেন। বাংলাদেশকে বাংলার মানুষকে ভালবাসার অপরাধে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আর রাজাকারের হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। বিশিষ্ট সমাজকর্মী অ্যারোমা দত্ত সেই পরিবারেরই উত্তরসুরী।
৫
“যুক্তি তক্কো আর গপ্পো”-তে তিনি যখন বলেন, “সে দেখা যাবে নে চাইড্ডা”, সে যেন তার বুকের গভীর থেকে বেরিয়ে আসা স্বগতোক্তি। পুরোপুরি পূর্ববাংলার ভাষায়, ভঙ্গিতে, টানে। এ যেন ঠিক তার জীবনদর্শন। ঋত্বিক ভবিষ্যতের ধার ধারতেন না। পরিকল্পনা করার বিলাসিতা তার ছিল না। মানুষের দুঃখ-দুর্দশার সামনে সেটা তুচ্ছ। আজ মানুষের পাশে দাঁড়ানো দরকার, আজ অবিচারের বিরুদ্ধে কথা বলা দরকার; ঠিক এই মুহূর্তেই। ভবিষ্যৎ? “সে পরে দেখা যাবেনে।”
তিনি নিজেই বলেছিলেন, “মানুষের সঙ্গে কথা বলার জন্য যদি আরও ভালো কোনো মাধ্যম পাই, আমি ক্যামেরা লাথি মেরে ফেলে দেব।” শুনলে মনে হয়, তিনি সিনেমাকে খুব একটা গুরুত্ব দিতেন না। অথচ তাকে বাদ দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্র ভাবাই যায় না। তার ভিজ্যুয়াল ব্যাকরণে, তার রাজনৈতিক বক্তব্যে, ঋত্বিকের দুর্দান্ত প্রভাব।
শুধু কি তাই, ঋত্বিক-পরবর্তীরা সবাই এই শিল্পের দীক্ষা নিয়েছে তার কাছে। কেউ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে, কেউ কর্মক্ষেত্রে, কেউ তাকে দেখে, বাকিরা তার সিনেমা দেখে। এমনকি যারা তার একটাও সিনেমা দেখেনি, তাদের কাজেও কোথাও না কোথাও তার প্রভাব থেকেই যায়। তাদের সিনেমায়, শিল্পীস্বত্বায়, মেরুদণ্ডের কশেরুকায় শক্তি যোগায় ঋত্বিক।
৬
ঋত্বিক মানুষের পরিচালক। সিনেমার ব্যবসা নিয়ে তার বেশি মাথাব্যথা ছিল না। খ্যাতি, সম্মান, পুরস্কারে ছিলও না তেমন আগ্রহ। তার আকর্ষণ ছিল মানুষের প্রতি, শোষিতের প্রতি, দেশভাগে ছিন্নমূল হয়ে যাওয়া লাখো জীবনের প্রতি। তাদের প্রতি তার ছিল তীব্র দায়বোধ। বাংলা চলচ্চিত্রে যে কেউ যখন আজ ভাষা, ইতিহাস, রাজনীতি নিয়ে কথা বলে, তার চেতনার গভীরে কোথাও না কোথাও ঋত্বিকের অচিন ছায়া লেগে থাকে।
আর সে মানুষটি, যদিও আমরা ভুলে যাই, এই বাংলাদেশের সন্তান। এই বাংলাদেশের মাটি, এই বাংলাদেশের নদী-জল-হাওয়া তার ভেতরের শিল্পীস্বত্বাকে গড়ে তুলেছিল। দেশভাগ তাকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ছিন্ন করতে পারেনি। তার হৃদয়ের গভীরের বাংলাদেশ তাকে কোনোদিন ছেড়ে যায়নি। তিনি বারবার ফিরে এসেছেন বাংলার মানুষের কাছে। বাঙালির কাছে। বাংলাদেশের কাছে।
৭
কিন্তু ভালোবাসা কখনো একতরফা হয় না। হতে পারে না। ঋত্বিক ঘটক যে ভালোবাসা বাংলাদেশকে দিয়েছেন, দেশভাগের ক্ষত সয়েও, সেই ভালোবাসার প্রতিদান বাংলাদেশ দেবে না? তার এই খেপা সন্তানকে ভালো না বেসে উপায় কি বাংলা মায়ের! তাকে ছাড়া যে বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস পূর্ণ হয় না। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস পূর্ণ হয় না। তিনি যেভাবে অবলীলায় পরম আবেগে রুপালি পর্দায় উচ্চারণ করেন ‘বাংলাদেশ’, সে আবেগ ফিরিয়ে না দিয়ে উপায় কি বাংলাদেশের!
বাংলাদেশের তাকে ভালোবাসতেই হবে!